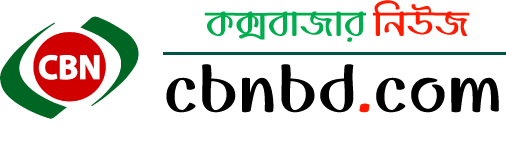অধ্যাপক রায়হান উদ্দিন
আমাদের এই উপমহাদেশে বাংলা, উর্দ্দু, অসমিয়া, গুজরাটি, তামিল তেলেগু ফার্সী প্রভৃতি বহু ভাষার বই বন্ধ করা হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের “যুগবাণী’ বইটি ইংরেজ তার ক্ষমতার বলে ১৯৩১ সালে বাজেয়াপ্ত করে।ইংরেজ আজ বিতাড়িত, নজরুলও পরলোকগত। তবুও অমর তাঁর সেই বই এবং বই এর প্রত্যেক কবিতা। উনি এসেছেন মানুষকে ভালোবাসতে এবং ভালোবাসার জন্য জীবন দিতে রাজী আছেন। উনি জেল খেটেছেন । তাঁকে কিন্তু অফার দেওয়া হয়েছিল।যিনি তাঁর বিচারক ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সী মেজিস্ট্রেট মি: সুইন হো। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের উনি ২৭ বছর বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন।
নজরুলকে ক্ষমা করে দেওয়ার একটি অফার দেওয়া হয়েছিল। তখন “রাজবন্দীর জবান বন্দী” এবং কি সেই জবানবন্দী? এটি পড়লে এমনি মাথা উচু হয়। বুক ফুলে উঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে “বসন্ত“ উৎসর্গ করতে গেলেন, তখন ঐ জেলার বলেছিলেন, “ইজ দিজ ক্রিমিনাল সো গ্রেট এ ম্যান? তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন , নজরুল জগৎ কাঁপিয়ে দেওয়ার একজন মানুষ। সকল বিধি বিধান ,তথাকথিত শৃঙ্খলভেঙ্গে , বাধন এবং ভয়কে জয় করতে এসেছিলেন নজরুল। বীর কবি নজরুলের একটি নয়, অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যেমন ‘ভাঙার গান’ ‘বিষের বাঁশী’ ‘চন্দ্রবিন্দু’ প্রভৃতি। সবাই বুঝতে পারে কবির প্রত্যেক বই বাতিল করা হবে- উদ্দেশ্য লেখার জগত থেকে কবিকে সরিয়ে দেওয়া। তখন ইংরেজরা জনসাধারণের উত্তেজনা দেখে ১৯৪৫ সালে ৩০ শে নভেম্বর সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ বইটি বাতিল হয়। কথাশিল্পী খুবই দু:খ পান। তিনি অনেককে অনুরোধ করেন যাতে তাঁর বইটি মুক্তি পায়। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তিনি পত্র লিখেন যাতে বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বইটি বাতিল হওয়ার পরে কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রথম সম্মেলন হচ্ছিল। সে সময় তার চিন্তায় কি এসেছিলো তা শিশির করের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, “আচ্ছা তোমাদের এটা তো সারা বাংলার লাইব্রেরীর ব্যাপার। তোমরা একটা কাজ করনা, আর তোমাদেরতো এটা কাজ। এই যে সরকার আমার পথের দাবীকে আটকে রেখেছে, এটা সভা থেকে এর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে। সরকারের টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করতো তাহলে আমার এত দু:খ হতো না। ”দু:খের বিষয় কথাশিল্পী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সে বইটির শুভমুক্তি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পার ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি আলবার্ট হলে তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয় এবং পথের দাবী বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাব করেন অনুল চন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক সুরেন্দনাথ গোস্বামী ও বঙ্কিম সেন সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। তখন শেরে বাংলা ফজলুল হক এর মন্ত্রিত্ব চলছিল। বাংলা ১৩৪৬ সময়ে বইটির দ্বিতীয় সংস্করন ছাপা হয়।
আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র কবিগুরুকে তাঁর বই অবমুক্ত করনের জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। আচ্ছা শরৎচন্দ্র কবিগুরুকে পত্র দিবেন কেন? তিনিতো ইংরেজ বড়লাঠকে পত্র দিতে পারতেন। তাহলে শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল ইংরেজকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের উপর সন্তুষ্ট রেখেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ রাজী হলেই ইংরেজও রাজী হতে পারে।সেই সময় স্বরাজ আন্দোলনের ঢেউ এতো বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, মানুষের ফাসি হচ্ছিল, জেল হচ্ছিল, চাবুক খেতে হচ্ছিল, মা বোনদের ইজ্জত হারাতে হচ্ছিল। আবার ভারতীয়রা ইংরেজদের খতম করছিল। বোমা মারছিল, ইংরেজপুস্ট দালালদের ঘরে হানা দিয়ে বিপ্লবীরা টা্কা পয়সা ধন দৌলত নিয়ে নিচ্ছিল। তখন যারা মেরেছেন , মরেছেন তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় অমর। যারা নিরপেক্ষ ছিলেন ইতিহাসে তারা আজ অপাংক্তেয়। আর যারা বিরোধীতা করেছেন তারা বিশ্বাসঘাতক। সমাজ বিরোধীরা, খুন জখম করে যেমন অপরাধী হয়, রাজনৈতিক নেতাদের স্বাধীনতার নামে হত্যা লুঠপাঠকেও রবীন্দ্রনাথ সে রকম সমান অপরাধ মনে করতেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ‘দন্ডনীতি’,প্রবাসী’ আশ্বিন ১৩৪৪) শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের জন্য লিখেছেন, আন্দোলন করতে , খুনজখম , লুঠপাটের জন্য যারা দায়ী তারাও অন্যান্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি মনে করতেন। (বাঙালীর রাস্ট্রচিন্তা, ৩৪৮ পৃস্টা) ১৯২২ সালে কবিগুরুর “শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে (রুরাল রিকন্ট্রাকসন) বা পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন লেনার্ড কে , এম্মহার্স্ট। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংরেজদের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে অর্থ সংগৃহিত হয়। (বাঙালীর রাস্ট্রচিন্তা, পৃ:৩২৭) গান্ধীজীর চরকা তত্ত্বের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।রবীঠাকুরের মতে “স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে। চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণ পথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্র বুদ্ধির পথে”(রবীন্দ্র রচনাবলী ‘স্বরাজ সাধন’,খন্ড ১৩ পৃ;৩৪৩) গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতি তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নি। তার মতে, “বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতি বিদ্বেষই প্রকাশ পায়; তাই সেই নীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি। (কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী খন্ড ১৩ পৃ:৩০৩)।
কেন কবিগুরুকে শরৎবাবু তাঁর বই মুক্ত করার জন্য ইংরেজকে অনুরোধ করতে বললেন? শরৎবাবু একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া ‘পথের দাবী’ বইটি উপহার দেন এবং তাঁর মতামত চেয়ে পত্র দিতে অনুরোধ করেন। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দেন তা এই ……
“কল্যাণীয়েষু,
তোমার ‘পথের দাবী’ পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজনক। অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্যে হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে – কারণ লেখক যদি ইংরাজ রাজকে .. মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাই পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম- আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম- একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্ত সেই পরের সহায়তার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র – তাই ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে যদি কর্তব্যের খাতিরে দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়, তাতে প্রমাণ হয়েছে মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে পূজা করি – ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হতোনা।আমরা রাজা হলে যে হতোই না, সে আমাদের জমিদারের ও রাজণ্যের বহুবিধ ব্যবহারে আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যিকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনিই ঘটবে – রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নি:সন্দেহে জেনেই ঘটেছে।
তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত – কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশ ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই – অপরিণত বয়সের বালক – বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিতে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মুল্য – আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মুল্য একেবারেই মাটি করে দেয়া হয়।
ইতি ২৭শে মাঘ ১৩৩৩।
-তোমাদেরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”
এর উত্তরে শরৎবাবু যে চিঠির খসড়া করেন, যেটি উমাপ্রসাদবাবুর সৌজণ্যে প্রাপ্ত, সেটি ‘দরদী শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত আছে:
“সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হওড়া
শ্রীচরণেষু,
আপনার পত্র পেলাম। বেশ তাই হোক। বইখানি আমার নিজের বলে একটুখানি দু:খ হবার কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তাতে আমার অভিমান নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্মন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।
আপনি লিখেছেন , ইংরেজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেস্টা করতাম তাহলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানত: তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ান দের প্রোপাগান্ডা হত , কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাংলাভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখেনা। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই এর সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভাণ করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাব অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না, আজও নেই। তাদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই। সুতরাং দু’দিন আগে পাছের জন্য কিছু যায় আাসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু বাঙলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় তো করতেই হবে – তা’ মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দন্ড আছে এবং মনে করি প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এজন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথা ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।
চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় এর জন্য হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ডালা কন্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।
কিন্তু বই খানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি তা বলত পেরেছি, কিন্তু এটাই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এ ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।
আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মতো সহিঞ্চুতা নেই। একথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করার জাসটিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাসটিফিকেশন ও তেমনি আছে।
আমার প্রতি আপনি অবিচার করেছেন যে আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সে ফাঁকে গা ঢাকা দেয়ার চেস্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু হইচই করে নয়, আর একখানা বই লিখে।
আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যান্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে একটু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যিকার কল্যাণ নেই, সে আমার শান্তনা হতো। মানুষের ভুল হয়েছে মনে করতাম।
আমি কোনরুপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি। যা মনে এসেছে তাই অকপটে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকত আমি চুপ করে যেতাম। আমি সত্যিকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এল, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছা হয়।
উত্তেজনা ও অজ্ঞতাবশত: এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রুঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন সুতরাং কথায় বা আচরণে লেশমাত্র ব্যথা দেয়ার কথাটা আমি ভাবতেও পারিনি।
ইতি- ২ রা ফাল্গুন, ১৩৩৩, সেবক, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।”
শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা’ গ্রন্থ হতে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। শরৎ চন্দ্র স্বয়ং লিখেছেন: “সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি ‘পথের দাবী’পড়ে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন! আমার ‘পথের দাবী’ পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এ দিকটাই বড় হয়ে থাকে তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা, কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয়ই এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার ‘পথের দাবী’র যে এত বড় লাঞ্চনা হবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা’ কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।।”
কবি রবীন্দ্রনাথের চিঠি মন দিয়ে পড়লে, আর শরৎবাবুর পত্র মন দিয়ে পড়লে তাতে কে কতটা ইংরেজ প্রেমিক কে কতটা ইংরেজ বিরোধী ঠিক করতে পারা যাবে। কে সাহসের সাথে শাস্তি নিতে বেপরোয়া, আর কে ইংরেজের প্রশংসা ও মুক্তির জয়গাথা গাইছেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। সে সময় ভারতবাসীকে ইংরেজরা হাজারে হাজারে গাছের ডালে বেঁধে ফাঁসি দিচ্ছে, মা বোনদের ইজ্জত হরণ করছে, করছে প্রাণ সংহার, দিচ্ছে কারাদন্ড, যাবজ্জীবন-সে সময় দিল্লীর রাজপ্রাসাদে সমগ্র ভারতের ইংরেজ নেতা সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। ঠিক সে সময় যদি তাঁর তোষণ ও তোয়াজে কেউ কোন কবিতা লিখে উপহার প্রদান করেন তাকে বর্তমান ভারতবাসী কোন দৃস্টিতে দেখবেন কে জানে! মনে হয় মন্দ ধারনাই পোষন করবেন।
কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ এর জন্য প্রশংসা ও স্তবস্তুতিপুর্ন কবিতা লিখে তাঁর পদপ্রান্তে উপহার দিলেন।
সেটা কোন কবিতা ছিল , যাঁরা জানেন না, শুনলে চমকে উঠবেন, সেটাই হচ্ছে- ‘জনগণমন অধিনাযক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা…….!